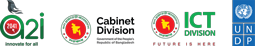- আমাদের সম্পর্কে
- আমাদের সেবা
-
নীতিমালা
পুস্তক ধার প্রদান নীতিমালা
ইন্টারনেট ব্যবহারের নীতিমালা
বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন সরবারাহ সংক্রান্ত নীতিমালা
জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি
-
অন্যান্য কার্যালয়
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর
জাতীয়/বিভাগীয় কার্যালয়
বিশেষ গণগ্রন্থাগার
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারসমূহ
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহ
- ই-সেবা
-
ফরম
বেসরকারি পাঠাগার নিবন্ধন ফরম
রেফারেন্স সেবা ফরম
পুস্তক লেনদেন সদস্য ফরম
-
গ্যালারি
ফটো গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
-
যোগাযোগ
অফিস যোগাযোগ
গুগল ম্যাপ
- মতামত
-
নতুন অন্তর্ভুক্ত বই
তালিকা
প্রচ্ছদ
-
জুলাই স্মৃতি উদযাপন অনুষ্ঠানমালা
জুলাই স্মৃতি উদযাপন অনুষ্ঠানমালা
-
জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালার টিভিসি/ভিডিও/ডকুমেন্টারি
টিভিসি/ভিডিও/ডকুমেন্টারি
গ্রন্থাগার সমাজ উন্নয়নের বাহন। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালনপালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা উন্নয়নের মূল ভিত্তি। শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ উন্নয়নমনস্ক হয়। গ্রন্থাগার শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ গ্রন্থাগারে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। তাই গ্রন্থাগারকে বলা হয় ‘জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়’। ‘লাইব্রেরি’ শব্দের বাংলা অর্থ ‘গ্রন্থাগার’। আর ‘গ্রন্থাগার’ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো গ্রন্থ+আগার=গ্রন্থাগার। অর্থাৎ, গ্রন্থাগার হচ্ছে গ্রন্থের আগার বা সংগ্রহশালা। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং মানুষের পাঠের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ যে ঘরে রাখা হয় তাই গ্রন্থাগার। তবে গ্রন্থাগারে গ্রন্থের পাশাপাশি নানারকম পত্রপত্রিকা এবং খেলাধুলার সামগ্রীও থাকে।
লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথাÑব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সর্বজনীন। যে লাইব্রেরি সমাজের সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত এবং সমাজের সব মানুষের পছন্দের কথা বিবেচনায় রেখে যেখানে গ্রন্থ নির্বাচন করা হয় তা সর্বজনীন লাইব্রেরি। স্কুল-কলেজের লাইব্রেরিতে পাঠ্য বিষয় ও পাঠ-সহায়ক বিষয়ের পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর লেখা বই এবং বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকী রাখা হয়। সাহিত্য চর্চার জন্য কল্পনাশক্তির পাশাপাশি প্রয়োজন বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুশীলন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে বলেন, সাহিত্য চর্চা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং সাহিত্য চর্চার জন্য লাইব্রেরি অপরিহার্য। প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপর স্থান দিয়েছেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘নিজের অস্তিত্ব ও স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা, অবশ্য নিজের অস্তিত্ব ও স্বজাতির বিশেষত্ব তথা ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং দেশীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং এসবের বিকাশ সাধনে লাইব্রেরির ভূমিকা অপরিহার্য।
প্রাচীনযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল, তার মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাগদাদ, কর্ডোভা ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিপুলায়তন গ্রন্থাগারগুলো সারা জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশ পুরনো। প্রথম দিকে মানুষ নিজের ঘরের কোণে, মন্দির মসজিদ উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে গ্রন্থ সংরক্ষণ করতে শুরু করে। রোমে প্রথম সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এটি স্থাপিত হয়। রোম ছাড়াও প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, মিসর, চীন, ভারত ও তিব্বতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মুসলমানদের শাসন আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে স্পেনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশটিতে বিশ্বের গুণী জ্ঞানীদের মিলন মেলার তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সভ্যতার অন্যতম উপাদান হলো গ্রন্থ। দেহের পুষ্টি জোগায় খাদ্য, আর বই জোগায় মনের খাদ্য। তাই ‘বই’ সভ্যসমাজের মানুষের নিত্যসঙ্গী। জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে গ্রন্থ। লেখক লেখেন, প্রকাশক ছাপেন, বিক্রেতা বই বিক্রি করেন আর গ্রন্থাগারিক তা সংগ্রহ করে যথাযথ বিন্যাস করেন এবং পাঠক সমাজ যথাসময়ে ওইসব উপাদান থেকে মনের খোরাক এবং জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।
বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় মানুষের কল্পনাপ্রসূত চিন্তাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ মানুষকে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলো যেমন ছাত্রদের বিজ্ঞান গবেষণায় সাহায্য করে তেমনি নব নব আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। ছাত্র-শিক্ষক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন। অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক প্রতিদিনের টিফিন পিরিয়ড বা অন্য অবসর সময়টা আড্ডা ও গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা লাইব্রেরি থাকলে ছাত্র-শিক্ষক তাদের প্রতিদিনের অবসর সময়টা পড়ালেখায় কাটাতে পারে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। স্বাধীনভাবে সৃজনশীল জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বন্ধুর মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। গ্রন্থাগার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্থাপিত হয়। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সবশ্রেণির মানুষই উপকৃত হয়। কম লেখাপড়া জানা ও গরিব মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অভাবনীয়। গ্রন্থাগারে থাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠকের জন্যে গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জনের যে সুযোগ করে দেয়, সে সুযোগ অন্য কোথাও নেই। গ্রন্থাগার গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহশালা, যা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করে জ্ঞানের মণিমুক্তা সংগ্রহের সুযোগ পায়। গ্রন্থাগারের আয়োজন সর্বসাধারণের জন্যে অবারিত। চিন্তাশীল মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনেক বেশি। গ্রন্থাগার জ্ঞান আহরণের সহজ মাধ্যম। আমাদের মতো গরিব দেশে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, মৌলিক চাহিদা মেটাতেই আমরা হিমশিম খাই। তাই আমাদের পক্ষে বই কিনে পড়া অনেক সময় সম্ভব হয় না।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবইয়ের বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা শিক্ষার্থীর নেই। এ পদ্ধতি তাকে স্বশিক্ষিত তো করেই না; বরং স্বশিক্ষিত হওয়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। কিন্তু গ্রন্থাগার সবার জন্যই মুক্ত ও অবাধ এবং সব ধরনের গ্রন্থের সমাহার থাকে। পড়বার স্বাধীনতা এখানে অফুরন্ত। একটি পক্ষপাতমুক্ত সমাজ গড়ার সহায়ক শক্তি লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক। গণতন্ত্রের সাফল্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকা টেলিভিশন, রেডিও, প্রচার মাধ্যম কোনোটার চেয়ে কম নয়। আধুনিক বিশ্বে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাই বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে আসছে। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগার, ওয়াশিংটনের সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলোর অন্যতম।
গ্রন্থাগার শুধু সমাজসংস্কারের কাজই করে না, তা সমাজের সামগ্রিক বিকাশের স্থায়ী উপকরণ হিসেবেও ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগার সবার জন্য উন্মুক্ত। গ্রন্থাগারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করে গ্রন্থগুলো বিন্যস্ত করেন, ক্যাটালগ তৈরি করেন। বর্তমান বিশ্বে ডিউই পদ্ধতি বা দশমিক পদ্ধতিতে বইয়ের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। গ্রন্থাগার থেকে বই খুঁজে পেতে এই পদ্ধতি বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব নিয়ম মেনেই পাঠককে বই পড়তে হয়।
প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেই জন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব তত বেশি উপকৃত হব। আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়। দেখা যায়, এমনকি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়, প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর দুটি। কাজেই আমাদের দেশে হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও স্থাপন করতে হবে।
লেখক : সতীর্থ রহমান, সহকারী শিক্ষক, নুনসাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিনাজপুর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস